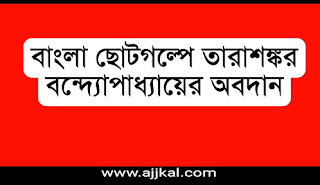বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান | Tarashankar Banerjee’s Contribution in Bengali Short Stories
❏ প্রশ্ন:- বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর (Tarashankar Banerjee’s Contribution in Bengali Short Stories)।
উত্তর:- বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন প্রকৃত বড় শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) অন্যতম। কথাসাহিত্যে তাঁর পূর্ণশক্তিধর প্রতিভা। বিংশ শতাব্দীর শিল্পী হয়েও তিনি ঐতিহ্যানুসরণ থেকে বঞ্চিত হননি। আধুনিক হবার কোনো বিশিষ্ট বাসনা তাঁর ছিল না। উচ্চকণ্ঠে স্বাতন্ত্র্যঘোষণা, শৌখিন মজদুরি কিংবা কারুসর্বস্বতা থেকে তিনি স্বযত্নে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন ঠিকই, তবু বর্তমান যুগের তরঙ্গ সঙ্কুলতা তিনি উপলব্ধি না করে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের পর জনপ্রিয়তা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক। ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে তারাশংকরের আবির্ভাব ঘটেছিল।
কিন্তু ‘কল্লোল’ -এর গুটি কাটিয়ে উন্মুক্ত আকাশে উড়তে তাঁর বিলম্ব হয়নি। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশে তিনি একটা বিস্ময়কর প্রাণশক্তির অধিকার লাভ করেছিলেন। আর একদিকে দেখেছিলেন সামন্ত্রতান্ত্রিক শক্তির শেষ প্রতিনিধি জমিদারতন্ত্র ভেঙে পড়েছে, সেখানে আসর জাঁকিয়ে বসেছে কলকারখানা, যন্ত্রাসুর, মিল মালিক, ম্যানেজার শ্রমিক।
অন্যদিকে তিনি দেখছেন, পুরাতন জরাজীর্ণতার সঙ্গে নবীন প্রাণশক্তির দ্বন্দ্ব। বিগত জীবন তার ভগ্ন বিধ্বস্ত বাস্তুভিটায় কোনো প্রকারে পড়ে আছে। আধুনিক জীবন উচ্চহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ করে নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করছে। তারাশংকরের উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘রাইকমল’, ‘কবি’, ‘কালিন্দী’, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, ‘নাগিনীকন্যার কাহিনী’, ‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘উত্তরায়ণ’, ‘জবানবন্দী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ‘গল্পসংগ্রহ’, ‘জলসাগর’, ‘বেদিনী’, ‘কামধেনু’ প্রভৃতি বহুপঠিত সর্বজননন্দিত গ্রন্থ।
কাহিনীর বিশালতা চরিত্রের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য এবং মানব জীবন সম্পর্কে একটা বিশুদ্ধ দার্শনিকবোধ তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে সমকালীন সমস্ত কথা সাহিত্যিকের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। তাঁর রচনায় বর্ণনাগত শিথিলতা যে নেই তা নয়, কোনো কোনো জায়গায় অনাবশ্যক মন্তব্য ও দার্শনিক চিন্তার গুরুভার উপন্যাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে ক্ষুণ্ন করেছে। তবু বিশ শতকের মধ্যভাগের বাঙ্গালী জীবনের সামগ্রিক পরিচয়, তার অন্তর্জীবন ও আত্মার নিগূঢ় স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তাঁর উপন্যাসের সাহায্য নিতেই হবে। তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টির একপ্রান্তে জমিদারী প্রথা, তার পূর্ব গৌরবের স্মৃতি এবং বর্তমান ক্ষয়িষ্ণুতার বেদনা নিয়ে উপস্থিত, অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার অপরিহার্য আগমন সম্পর্কেও সচেতন।
সমাজতন্ত্রের মধ্যেও একসময়ে তিনি মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন। তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। জীবনের প্রত্যহকাম্য রূপের মধ্যে ডুব দিয়েই তিনি তৃপ্ত। দেহ – মন – প্রাণধারী মানুষের স্ট্র্যাজেডিতেই তিনি কাতর। কোনো রোমান্টিক অনির্দেশ্য বেদনায় তিনি ভারাক্রান্ত নন। ‘ধাত্রী – দেবতা’ থেকে শুরু করে ‘নাগিনীকন্যার কাহিনী পর্যন্ত বিস্তৃত কালখণ্ডে তারাশঙ্কর সৃষ্টি ক্ষমতার চরমে পৌঁছেছিলেন। কোনো কোনো উপন্যাসে একটা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক চিত্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কাহার বাউরিদের সমাজ, সাপুড়ের পল্লী, ঝুমুরের দল, তাদের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু গোষ্ঠীগত নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চরিত্রসৃষ্টিতেও তিনি আশ্চর্য নিপুণতা দেখিয়েছেন। এই মানুষগুলিকে লেখক যেন প্রত্যক্ষ জীবন থেকে এনে ভাষা – ভঙ্গিসমেত উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি জীবনদ্রষ্টা ও ভাষ্যকার স্রষ্টার ভূমিকায় সন্তুষ্ট না থেকে দার্শনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।
তারশংকরের অসংখ্য ছোটগল্প মূলত জীবনেরই জয়গান। তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থগুলি হল— “পাষাণ পুরী’, ‘নীলকণ্ঠ’, ‘ছলনাময়ী’, ‘জলসাঘর’, ‘রসকলি’, ‘তিনশূন্য’, ‘প্রতিধ্বনি’, ‘বেদেনী’, ‘যাদুকরী’, ‘স্থলপদ্ম’, ‘হারানো সুর’, ‘তারিনী মাঝির গল্প’, ‘অগ্রদানী’, ‘কাক পণ্ডিত’, ‘না’, ‘নারী ও নাগিনী’ ‘পৌষলক্ষী’ ‘কালা পাহাড়’ ‘আখডাই এর দীঘি’, ‘শ্মশান বৈরাগ্য’ ‘সাড়ে সাতগড়ার জমিদার’, তাসের ঘর’, ‘ডাক হরকরা’, ‘মতিলাল’ প্রভৃতি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। তারাশংকর যথার্থ জীবনশিল্পী। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন। এই সব গল্পে তিনি সমাজের যে বিচিত্র শ্রেণীর চরিত্র এঁকেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তার চরিত্রগুলির কেউ জমিদার, কেউ গোমস্তা, কেউ পণ্ডিত, কেউ লোভী ব্রাহ্মণ, কেউ বৈষ্ণব, কেউ ঠগ, কেউ চাষী, কেউ অন্ধ। তারাশংকর চরিত্র ও ঘটনা বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন।