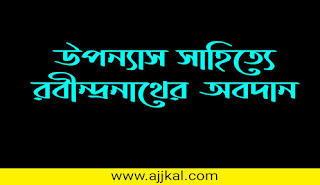উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান | Rabindranath’s Contribution to Novel Literature
❏ প্রশ্নঃ- রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (Rabindranath’s Contribution to Novel Literature)
উত্তর:- রবীন্দ্রনাথ কবি সার্বভৌম। মূলত কবি হলেও সাহিত্যের সর্বভূমিতে তার গৌরবোজ্জ্বল অধিষ্ঠান। বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসে তিনিই প্রথম যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শই অবলম্বন করেছিলেন। ‘বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭) উপন্যাস দুটি ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস যাদের মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষার চেয়ে হৃদয় ধর্ম প্রকাশের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, প্রখ্যাত গবেষক সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণীয়, “রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার গোড়ার দিকে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা উপন্যাস বা তথাকথিত ‘রোম্যান্স’ (romance) লিখতেন, তাঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী অবাধ কল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র সেই অবাধ কল্পনাকে বস্তুভিত্তিক তথ্য ও শৃঙ্খলাপূর্ণ কল্পনার দ্বারা সংযত করে তাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য কর্মে নিয়োগ করেছিলেন।
কিন্তু স্বল্প প্রতিভার লেখকদের সে শক্তি ছিল না, তাঁরা ইতিহাসকে ছাড়িয়ে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে উন্মত্তভাবে ধাবমান হতেন। রবীন্দ্রনাথ যৌবনারম্ভে যেমন কাব্যজীবনে হৃদয় বাষ্পপূর্ণ কল্পনার আর্দ্রভূমি পার হয়ে পায়ের তলায় মাটি পেলেন, তেমনি ‘করুণা’ র আবেগতরল দুর্বল কাহিনী ছাড়িয়ে ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাহিনীকে বস্তুভিত্তিক কল্পনার জগতে মুক্তি দিলেন।” তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এর মধ্যে বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য ও বিভার যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা ইতিহাসে অনুল্লেখিত। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটি, ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।’ “এতে কল্পনার বৈচিত্র্য থাকলেও লেখক ইতিহাসকে বড়ো কোথাও অতিক্রম করেননি।
শেষ দিকে তো তিনি উপন্যাসের কাহিনীকে পুরোপুরি ইতিহাসের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের প্রচলিত আদর্শ ত্যাগ করে প্রধান চরিত্রকে যথার্থ স্বরূপে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এর ফলে প্রতাপাদিত্য হয়ে পড়েছেন উদ্ধত অবিনয়ী মূঢ় নির্মম ও অপরিণমদর্শী।”
এরপর রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক উপন্যাস ত্যাগ করে আধুনিক জীবনের বাস্তব জটিল সমস্যাভিত্তিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন। একে একে প্রকাশিত হল “চোখের বালি” (১৯০৩), ‘নৌকাডুবি’ (১৯০৬), ‘গোরা’ (১৯১০), ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ‘ঘরে বাইরে (১৯১৩), ‘যোগাযোগ’ (১৯১৯), ‘শেষের কবিতা’ (১৯১৯), ‘দুই বোন’ (১৯৩৩), ‘মালঞ্চ (১৯৩৪), ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস রচনার ১৩ বছর পর ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বালবিধবা বিনোদিনীর হৃদয়ে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ ও তার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন।
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনো-বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস হিসাবে এটি স্মরণীয়। “মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী — দুজন পুরুষ দুজন স্ত্রীলোকের সমস্যা কিভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থিমোচন হল; বাঙলা সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগসঞ্চিত সংস্কারে কবিগুরু, কিভাবে আঘাত দিলেন, তার এক বিচিত্র বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা এই উপন্যাসে পাওয়া যাবে। … রবীন্দ্রনাথ বালবিধবার প্রেমকে স্বীকার করতে পারেননি, আবার তাকে সমাজ সংসারের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অবচেতন সত্তার নিগূঢ় ইঙ্গিত, সমাজ সংসারের স্বাভাবিক প্রকৃতির সংঘাতের ফলে নারীর জীবন কোন্ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিপূণতার সঙ্গে সে কথা বলেছেন।” পরবর্তী উপন্যাস ‘নৌকাডুবি’ কাহিনীর দিক দিয়ে অভিনব হলেও চরিত্রে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব নেই। এই উপন্যাসে পূর্ববর্তী মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি।
‘গোরা’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের পটভূমিকায় বিচিত্র জীবনসমস্যার উপস্থাপনা ও সমাধানে। “আকারে প্রকারে ভাবে আদর্শে গোরা মহাকাব্যের মতোই বিশাল — একটা গোটা জাতির মানসিক সঙ্কটের কাহিনী এর মূল বক্তব্য।” — এই উপন্যাসের নায়ক গোরা যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে গোটা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি।
গোরা প্রথমদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হলেও শেষদিকে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং যথার্থ ভারতীয়ত্বের স্বরূপ সে বুঝতে পেরেছে। ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় রেখেছেন। “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী আবহাওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তারই সঙ্গে দাম্ভিক দেশপ্রেম যা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ত্যাগ করে প্রচণ্ড লোভের মধ্যে সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়, তারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস রচনা করেন।… স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ, এই ত্রিভুজের কাহিনী মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ বিকর্ষণের সাহায্যে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।” ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বিপ্লবাদী নরনারীর শোচনীয় বিপর্যয়ের কাহিনী। “সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র, দেশসেবার নামে যে কোন অপকর্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিকূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে।”
রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাস আবার নবজন্ম লাভ করেছে ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার বিপূল তরঙ্গাঘাত বাংলা সাহিত্যকেও আলোড়িত করে তুলেছিল। মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তন, সামাজিক অবক্ষয়, শ্রমিক সমাজের জাগরণ, সামন্ততান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পতন, বণিক সমাজের উত্থান, যৌনতার সংক্রমণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালী লেখকরা নতুন ধরনের সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যকে প্রাচীনপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে দিতে উদ্যত হলেন। কল্লোলীয় লেখকগণ রবীন্দ্রবিরোধিতায় মুখর হলেন।
এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাস রচনার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি আধুনিক যুগের সকল লেখকের চেয়ে অনেক বেশী আধুনিক। প্রখ্যাত সমালোচকের ভাষায় “ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে রচিত কাব্যধর্মী ও রোমান্স আশ্রিত উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) একটি বিচিত্র বিস্ময়। তখন রবীন্দ্রনাথ সুবৃদ্ধ, কল্পনাবৃত্তির কিঞ্চিৎ খর্বতা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যৌবনমূর্তি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ‘শেষের কবিতায়’ যেন নতুন রামগিরি নতুন অলকাপুরীর অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন। প্রচুর কাব্যধর্ম, উৎকৃষ্ট গীতি কবিতার স্তবক এবং রোমান্সের উচ্ছ্বাস এই গ্রন্থকে ক্ষণে ক্ষণে গদ্যকাব্যে রূপান্তরিত করেছে।
অমিত লাবণ্যের প্রেমের আখ্যান এ কাহিনীর প্রধান উপাদান হলেও এর মধ্যে কবি একটি গভীর তাৎপর্য সংযোজিত করেছেন। দৈনন্দিন বিবাহিত জীবনের কর্তব্যপীড়িত গতানুগতিকতা এবং অপার্থিব রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসার এদুয়ের মধ্যে মিলন ঘটানো দুঃসাধ্য।… অপূর্ব কাব্যধর্মী বর্ণনা, তির্যক বাগবিন্যাসের নিপুণতা প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বর্গলোক রচনা এবং তা থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনের সকরুণ বেদনা বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের যৌবনমূর্তিকে এমন একটি অভাবনীয় ঐশ্বর্য দিয়েছে যে সেকালের তরুণ সম্প্রদায় যাঁরা ‘রবীন্দ্রযুগ চলে গেছে’ বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত হতচকিত হয়ে গেলেন।”