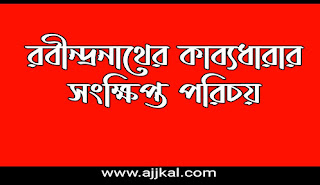রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার পরিচয় | Introduction to Rabindranath’s Poetry
❏ প্রশ্ন:- রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (Introduction to Rabindranath’s Poetry)
উত্তরঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কবি সার্বভৌম। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর পড়েছে। তথাপি তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় — তিনি কবি — কবিত্বই তাঁর জীবন ধর্ম। দীর্ঘ ৬০ বছরের বেশী সময় ধরে তিনি অজস্র কবিতা উপহার দিয়েছেন; যেগুলি ভাবের বিচিত্র লীলায়, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাষার অপূর্ব কারুকর্মে, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের লীলাবিলাসে; নিগূঢ় অধ্যাত্ম অনুভূতিতে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।
সাহিত্যের সর্বভূমিতে তাঁর অধিষ্ঠান হলেও তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় — তিনি কবি। রবীন্দ্রকবিমানসের বিকাশ ও উত্তরণ ঘটেছে ধীরে ধীরে নানা পর্বে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কাব্যিক পরিবেশে তাঁর কবিসত্তা আত্মপ্রকাশে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়’ ‘অভিলাষ’ কবিতা রচনার মাধ্যমে বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যিক আত্মপ্রকাশ। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ‘হিন্দুমেলার উপহার’ কবিতাটি হিন্দুমেলায় পঠিত হয়।
এরপর ক্রমশ তাঁর কাব্যসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশ কাল ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার কবি মানসেরও পরিবর্তন ঘটেছে। শৈশবে কবিজীবনের উন্মেষপর্বে জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখেছিলেন স্বপ্নরঙীন আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় দৃষ্টিতে, ক্রমশ তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে পরিবর্তন।
তাঁর কবিমানস সমৃদ্ধ হয়েছে প্রজ্ঞা, মনন ও দর্শনের সুগভীর উপলব্ধিতে। এই উপলব্ধির ফলে তাঁর কাব্যের পালা বদল ঘটেছে বারংবার। সীমা ও অসীমের লীলারহস্যের অবিরাম, পরিক্রমণ ঘটেছে তাঁর, কাব্যের রূপবৈচিত্র্য অপুরূপ ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংখ্যা ৫৪। এই সকল কাব্যে ধরা আছে তাঁর কবিমানসের বিচিত্র নানা বৈচিত্র্য। বারবার তাঁর কবিমানসের পালাবদল ঘটেছে, তাঁর প্রকাশ ঘটেছে কবিতার মধ্যে। রবীন্দ্র কবিমানসকে বিশ্লেষণ করলে বিশেষ কয়েকটি পূর্ব চোখে পড়ে।
❏ সূচনা পর্বঃ- রবীন্দ্র কবিমানসের সূচনা হয়েছে কতকগুলি কাব্য ও নাট্যধর্মী বাক্যের মাধ্যমে। এগুলি পড়লে বোঝা যায়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিচেতনার ক্রম জাগরণ ঘটছে। অনুভূতি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন প্রকৃতি ও মানবকে। রবীন্দ্রনাথ শৈশব ও যৌবনোন্মেষের প্রথম পর্বে লিখেছেন ‘বনফুল’ (১৮৭০), ‘কবিকাহিনী’ (১৮৭৭), ‘রুদ্রচণ্ড’ (১৮৭৮) ‘ভগ্নহৃদয়’ (১৮৮১), ‘শৈশব সংগীত (১৮৭৮)।
এই সূচনাপর্বের কাব্যগুলি আবেগ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হলেও এদের মধ্যে কবি প্রতিভার স্ফূরণ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। উচ্ছ্বাসপর্বে যে কাব্যগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে যৌবনের প্রথম আবেগ ও উচ্ছ্বাস— জগৎ ও জীবনকে দেখার এক রঙীন স্বপ্ন ও অনুভূতি এদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত।
এই পর্বে রয়েছে ‘সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), ‘প্রভাত সংগীত’ (১৮৮৩), ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’ (১৮৮২), ‘ছবি ও গান’ (১৮৮৪), ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) কাব্য। এই সকল কাব্যের কবিতার মধ্যে কবি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও অনিয়মিত আবেগের প্রাবল্য বেশি। এই পর্বের কবিতার মধ্যে কবিতার মানসমুক্তি ঘটেছে, কিন্তু শিল্পমুক্তি ঘটে নি।
এই পর্বে কবি পুরাতনকে অতিক্রম করে যেন নতুনকে আবাহন করতে চেয়েছেন। ‘সন্ধ্যাসংগীতে’ তিনি যেন প্রাণে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তা অনুভব করেছেন। এই স্বকীয়তা কখনো প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতি বর্ণনায়, কখনো হৃদয় বন্ধন মুক্তির উল্লাসে।
❏ মধ্য পর্বঃ- যৌবনে রবীন্দ্র মানসের পরিবর্তনের ফলে তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছে নতুন রূপ। যৌবন চেতনার আবেশে তিনি প্রকৃতির রূপ রস আকণ্ঠ পান করেছেন, তাকে প্রকাশ করেছেন স্বকীয় বিশেষ উপলব্ধির মাধ্যমে। মানবতা এসেছে তাঁর নতুন চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এই সঙ্গে কাবের মধ্যে তিনি শিল্পরস সংযোগেও সচেতন হয়েছেন। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে এই পর্বের কাব্যগুলি।
এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন‘ ‘মানসী’ (১৮৯০), ‘সোনার তরী’ (১৮৯৪) ‘চিত্রা’ (১৮৯৬), ‘চৈতালি’ (১৮৯৬), প্রভৃতি কাব্য। এই পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য মাধুর্য ও প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে, রূপ ও ভাবের মধ্যে ঘটেছে অপূর্ব সমন্বয়। এই পর্বে তাঁর রোমান্টিক শিল্প প্রতিভার আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে।
সম্ভবত তাঁর কবি – প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে এই পর্বে। ‘মানসী’ কাব্যেই রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ উদয়। তিনি এই পর্বে আপন কবিত্ব সম্পর্কে সচেতন। সার্থক ও ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দপ্রয়োগে ভাব ও কল্পনাকে মনোমত রূপ দিয়েছেন। প্রেমকে তিনি চিরন্তন সৌন্দর্যের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ‘সোনার তরী’তে এসে কবি প্রকৃতি ও মানুষকে কল্পজগৎ হতে সরিয়ে এনে তাদের সহজ সরল স্বাভাবিক রসমূর্তির মধ্যে স্থাপন করেছেন। ‘চিত্রা’ – কাব্যে কবি বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।
এই পর্বের কাব্যগুলি হল ‘কথা’ (১৯০০), ‘কাহিনী’ (১৯০০), ‘নৈবেদ্য’ (১৯০১), ‘খেয়া, (১৯১০), গীতাঞ্জলী ’(১৯১০), ‘গীতিমালা’ (১৯১০) ‘গীতালী’ (১৯১০) প্রভৃতি। কবি এই পর্বে প্রকৃতি ও মানবকে দূরে সরিয়ে রেখে ভগবানের বিচিত্র লীলাকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন। এই যুগটি হল ভগবানের সঙ্গে কবির অতীন্দ্রিয় লীলার যুগ। কবির অনুভূতিতে ভগবান বিরাট ও ঐশ্বর্যময়। ভগবানকে তিনি নিজস্ব অনুভূতির রসে ও রূপে অনুভব করেছেন। তিনি আবার প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও ভগবৎ-সাধনাকে অবলম্বন করে জীবনের পথ চলতে চেয়েছেন। জীবনের মধ্যপর্বে রবীন্দ্রমানসে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় দার্শনিক উপলব্ধি জন্মেছে।
এছাড়া এই সময় তাঁর মধ্যে মৃত্যু চিন্তা দেখা দিয়েছিল। এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে এই পর্বে। এই পর্বে রয়েছে ‘বলাকা’ (১৯১৬), ‘পূরবী’ (১৯২৫), ‘মহুয়া’ (১৯২৯), ‘পুনশ্চ (১৯৩২), ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫), ‘শ্যামলী’ (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্য। এই পর্বে রবীন্দ্র কবিমানস আবর্তিত হয়েছে দর্শন ও তত্ত্বভাবনায়। তিনি খোঁজার চেষ্টা করেছেন বিশ্বসৃষ্টির গতি ও প্রকৃতি, সৃষ্টির সঙ্গে ভগবানের নিগূঢ় সম্বন্ধ, মানবের প্রকৃত স্বরূপ, মৃত্যুর স্বরূপ অনিত্য জগৎ ও জীবনে নিত্যের নানা বিস্ময় ও রহস্য , প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপ। দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন এই পর্বে। কবি এই পর্বে দেখেছেন, জীবনের কোন কিছুই স্থির নয়, সব কিছুই দুরন্ত গতিতে ভেসে চলেছে কালস্রোতে। জীবন ও প্রকৃতি অবিরাম গতিশীল।
❏ অন্তিম পর্বঃ- জীবনসায়াহ্নে এসে কবির মনে নতুন এক চেতনা দেখা দিয়েছিল। এই সময় কবি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জগৎ ও জীবন তাঁর চোখে নতুন তাৎপর্যে ধরা পড়েছিল। এই পর্বে রয়েছে ‘প্রান্তিক’ (১৯৩৮), ‘সেঁজুতি’ (১৯৩৮), ‘আকাশ-প্রদীপ’ (১৯৩৯) ‘নবজাতক’ (১৯৪০), ‘রোগশয্যায়’ (১৯৪০), ‘জন্মদিনে’ (১৯৪১), ‘শেষ লেখা’ (১৯৪১) প্রভৃতি কাব্য। এই পর্বে ফেলে আসা দিনগুলির মধ্যে কবি আপন আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বুঝেছেন, মানুষের অন্তরাত্মা মহান ব্রহ্মের অংশ — ভূমার জ্যোতিমণ্ডলে তার নিত্য অবস্থান। দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও আত্মা অনন্ত — এই উপলব্ধি শেষ পর্বের কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে।
জীবনের এই পর্বে এসে কবি নতূন এক আশাবাদে উদ্দীপিত হয়েছেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন, জীবনে অন্ধকার শেষ কথা নয়, নতুন আলোকে দেশ জাগবে নব চেতনায় নবীন এক আগন্তুকের নেতৃত্বে। রবীন্দ্র কবিমানসে বারংবার কত যে নব নব অনুভূতির জন্ম হয়েছে, কত উপলব্ধির আলোছায়া তাঁর মনের আকাশে সঞ্চারমান, তার হিসাব কেউ কোন দিন দিতে পারবে না। বস্তুত রবীন্দ্রকাব্য যথার্থই এই কাব্য সমুদ্র।